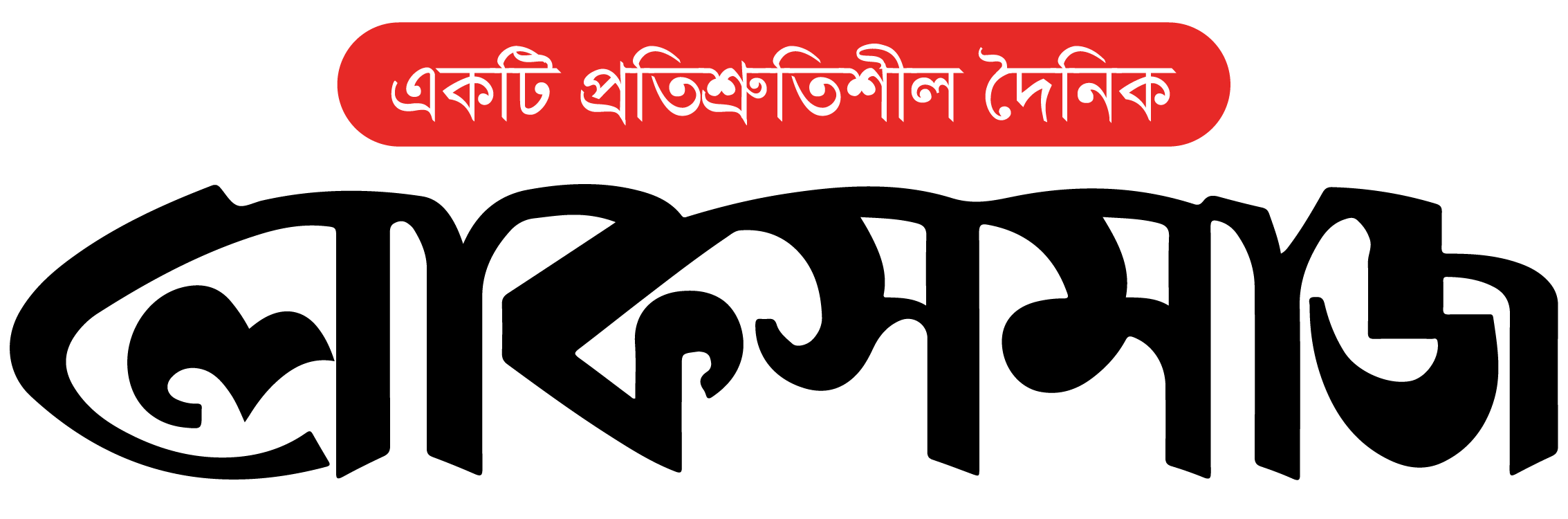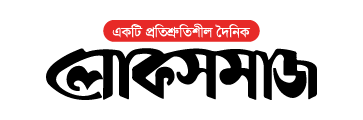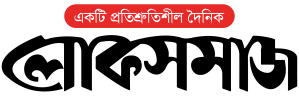ত্যাগ ও তিতিক্ষার
আনন্দ: ঈদুল আজহা
ড. শাহনাজ পারভীন
‘তার কাছে কি যায় পশু যায়? যায় না…
তার কাছে কি রক্ত, মাংস, চামড়া, হাড্ডি-
যায় কভু যায়? যায় না…
তার কাছে যায় তাকওয়া এবং আল্লাহভীতি
তার কাছে যায় ভালোবাসা প্রাণের প্রীতি
তার কাছে যায় লেগে থাকা তওবা এবং
ওয়াস্তাগফের এবং যে যায় দোযখ ভীতি।’
‘ঈদুল আজহা’ মূলত আরবি বাক্যাংশ। এর অর্থ হলো ‘ত্যাগের উৎসব’। এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ‘ত্যাগ করা’। কুরবানি হলো- কারো কাছাকাছি হওয়া। ব্যাপক অর্থে আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া। আবার ব্যক্তির সম্পদ, সময়, চেষ্টা, উদ্যম আল্লাহর বিধান মতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দেওয়াকেও আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি বলা হয়। ঈদুল আযহার দিনে মুসলমানেরা ফযরের নামাযের পর ঈদগাহে গিয়ে দুই রাকাত ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করেন এবং অব্যবহিত পরে স্ব-স্ব আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, দুম্বা ও উট আল্লাহর নামে কুরবানি করেন। ঈদুল আযহাকে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় কুরবানী ঈদও বলে থাকি। মুসলিম জাতির দুটি ঈদ। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। হিজরি শাওয়াল মাসের ১ তারিখে ঈদ-উল-ফিতর অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ঘটনাকে স্মরণ করে সারাবিশ্বের মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতি বছর জিলহজ মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে কুরবানি করেন। আরবি ‘কুরবানি’ শব্দটি ফারসি বা উর্দুতে ‘কুরবানি’ রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ ‘নৈকট্য’। মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য, মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করেন।

প্রথম নবী আদম আ. ও বিবি হাওয়া আ. এর সময় থেকেই কুরবানির প্রচলন। ইসলামের প্রথম কুরবানির প্রাচীন ইতিহাস পবিত্র কুরআনের হাবিল-কাবিলের ঘটনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। ইসলামের প্রথম কুরবানি এটি। হাবিল প্রথম মানুষ, যিনি আল্লাহর জন্য একটি পশু কুরবানি করেন। বর্ণনা থেকে জানা যায়, হাবিল একটি ভেড়া এবং তার ভাই কাবিল তার ফসলের কিছু অংশ স্রষ্টার উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। কুরবানি কবুলের নিদর্শন স্বরুপ সে সময় মহান আল্লাহর নির্ধারিত শরিয়ত বা পদ্ধতি ছিল এই যে, আকাশ থেকে আগুন নেমে আসবে এবং যার কুরবানি কবুল হবে তার জিনিস গ্রহণ করবে। অর্থাৎ অগুন সে জিনিসকে জালিয়ে ভষ্ম করে দেবে। সেই অনুযায়ী, আকাশ থেকে নেমে আসা নেককার হাবিলের জবেহকৃত পশুটির কুরবানি গ্রহণ করে। অন্যদিকে কাবিলের ফসলস্বরূপ প্রদত্ত কুরবানি প্রত্যাখ্যাত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেনÑ
‘আর তুমি তাদের কাছে আদমের দুই ছেলের (হাবিল-কাবিল) সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা কর, যখন তারা উভয়ে কুরবানি পেশ করলো। এরপর তাদের একজন থেকে কুরবানি গ্রহণ করা হলো আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হলো না। সে বললো, ‘অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো’। অন্যজন বলল, ‘আল্লাহ কেবল মুত্তাকিদের থেকে কুরবানি গ্রহণ করেন।’
(সুরা মায়েদা: আয়াত ২৭)
কুরবানি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন-
‘বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সব সৃষ্টির রব। তাঁর কোনো শরিক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি মুসলমানদের মধ্যে প্রথম’।
(সুরা আনআম : আয়াত ১৬২-১৬৩)
কুরবানির বিধান পরবর্তীতে মহান আল্লাহ নবী ও রাসুল মুসলিম জাতির পিতা, হজরত ইবরাহিম আ. কে স্বপ্নযোগে এ মর্মে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কুরবানি করার নির্দেশ দেন, ‘তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর নামে কুরবানি করো। হজরত ইবরাহিম আ. আদিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহর সন্তষ্টির জন্য ১০টি উট কুরবানি করেন। কিন্তু পুনরায় তিনি কুরবানি করার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হন। তখন তিনি আবারও ১০০টি উট কুরবানি করেন।
তারপরেও তিনি একই আদেশ পেয়ে ভাবলেন, আমার কাছে তো এ মুহূর্তে সবচেয়ে প্রিয়বস্তু হলো- পুত্র ইসমাইল আ.। এছাড়া আর কোনো প্রিয় বস্তু নেই। এরপর যখন সে তার (ইবরাহিম) সঙ্গে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছলো, তখন সে বললো, ‘হে প্রিয় ছেলে!, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবেহ (কুরবানি) করছি, অতএব দেখ (এতে) তোমার কী অভিমত’; সে (ইসমাঈল) বললো, ‘হে আমার বাবা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।’ (সুরা আস-সাফফাত: আয়াত ১০২)
তখন তিনি হজরত ইসমাইল আ. কে কুরবানি করতে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। যখন হজরত ইবরাহিম তার পুত্রকে কুরবানি দেওয়ার জন্য গলায় ছুরি চালানোর চেষ্টা করেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন যে, ইসমাইল আ. এর পরিবর্তে একটি প্রাণী কুরবানি হয়েছে এবং তার কোনো ক্ষতি হয়নি।
মহান আল্লাহ আবারও বলেনÑ
‘নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা’। আর আমি এক মহান জবেহের (কুরবানির) বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম। আর তার জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ইবরাহীমের প্রতি সালাম। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।’ (সুরা আস-সাফফাত : আয়াত ১০৬-১১০)
কুরবানি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন-
প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যেসব জন্তু তিনি রিজিক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও, যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।’
(সুরা হজ : আয়াত ৩৪-৩৫)

কুরবানি সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আবারও বলেছেন-
‘কিন্তু মনে রেখো! কোরবানির গোশত বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, আল্লাহর কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ তাকওয়া। এই লক্ষ্যেই কোরবানির পশুগুলোকে তোমাদের অধীন করে দেওয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শনের মাধ্যমে যে কল্যাণ দিয়েছেন, সেজন্যে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করো। হে নবি! আপনি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দিন যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না।’ (সুরা হজ : আয়াত ৩৭-৩৮)
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছির (র.) লিখেছেন: “মাংস বা রক্ত কোনটাই আল্লাহর কাছে পৌছায় না, পৌঁছায় তোমার মনের পবিত্র ইচ্ছা।”
কুরবানি কি বাধ্যতামুলক? এ বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে দু‘টো মত রয়েছে। কেউ কেউ এটাকে বাধ্যতামুলক মনে করেন,
কারণ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে – ‘অতএব আপনার রবের উদ্দেশ্যেই নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন।’
(সুরা কাউছার : আয়াত: ২)
আবার অনেকের সুর ভিন্ন। হাদীসে বর্ণিত আছে-
‘তোমাদের মাঝে যে কুরবানি করতে চায়, জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন কুরবানি সম্পন্ন করার আগে তার কোন চুল ও নখ না কাটে।’ (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৯৭৭)। তাঁদের যুক্তি ‘যে কুরবানি করতে চায়’ কথা দ্বারা বুঝা যায় এটা ওয়াজিব। বাধ্যতামুলক নয়।
বর্তমানে, মুসলমানদের মধ্যে পশু কুরবানির প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়। কে কত বড় এবং কত উচ্চ মূল্যের পশু কুরবানি করবে- তার এক অসম প্রতিযোগিতা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। মাঝে মাঝে এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় বিস্তর নিউজ ও প্রতিবেদন দেখতে পাই। কেউ আবার ফলাও করে উট বা দুম্বা কুরবানি দেন। উট হলো আরব দেশের পশু। তাই কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে- উট কুরবানিতে বেশি সওয়াবের অধিকারী হবেন।
মহান আল্লাহ ইব্রাহীম আ. কে স্বপ্নে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কুরবানি করতে আদেশ দিয়েছিলেন। মনোবিজ্ঞান, ধর্ম, জ্যোতিশাস্ত্র সহ সকল শাস্ত্র বলে স্বপ্ন হলো রূপক বিশেষ। আর ইব্রাহিমের বেলায় সে রূপকটির অর্থ ছিল তিনি আল্লাহকে কতটা ভালবাসেন তা পরীক্ষা করা। তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমানে আমরা যারা প্রতিযোগিতামূলক কুরবানিতে অংশ গ্রহণ করি, এর মাধ্যমে কি মহান আল্লাহর প্রতি সেই প্রগাঢ় ভালবাসা প্রকাশ পায়?
এখনও কেউ কেউ কুরবানির উদ্দেশ্যে গ্রামে আগে ভাগে কুরবানির পশু ক্রয় করে সারা বছর তাকে প্রতিপালন করে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ ধরনের অতি আদরের পশুটাকে জবাই করা বরং উত্তম কুরবানি। কারণ তখন সত্যি সত্যি একটা প্রিয় জিনিসকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করা হচ্ছে। যদিও বর্তমানে শহরের বাসিন্দাদের পশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকার কারণে আগে ভাগে পশু ক্রয় করা সম্ভব হয় না। ইসলামে, বিশেষ করে আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষদের কাছে পশু কুরবানির একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। তবুও, আত্মত্যাগই সব চেয়ে বড় কুরবানি।

আমাদের ছেলেবেলায় কুরবানিকে কেন্দ্র করে আমরা যে আনন্দ উল্লাস উপভোগ করেছি, বর্তমান সমাজে তেমনটি দেখা যায় না। আমাদের সময়ে আব্বা, চাচা, বড় ভাইয়েরা মিলে আশে পাশের হাটে গরু কিনতে যেতেন। আর আমরা ছোটরা বাড়িতে থেকে চাচাতো ভাইবোনরা মিলেমিশে গরুর জন্য ফুলের মালা, ঘাস লতা পাতা যোগাড় করে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। কখন আসবে গরু, কখন আসবে ছাগল। গরু ছাগল বাড়িতে আসা মাত্রই আমাদের ঈদের আনন্দ শুরু হয়ে যেতো। আমাদের ছেলেবেলায় কুরবানি ঈদের জন্য আলাদা করে তেমন ভাবে খুব একটা পোশাক পরিচ্ছদ কেনা হতো না বরং রোজার ঈদের বাড়তি জামাটাই কুরবানি ঈদের জামা হিসেবে রেখে দিতাম, মেনে নিতাম। এ নিয়ে আমাদের কোনো আফসোস থাকতো না, বরং আমরা ওই ক’টাদিন বড়দের সাথে কুরবানির গরু, ছাগল নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম। আনন্দ করতাম। কুরবানি ঈদের দিন সকালে মুরব্বিরা কুরবানির পশুকে সুন্দর করে গোসল করিয়ে সেমাই, সুজি না খেয়েই রেওয়াজ মতো অর্ধেক রোজা রেখে নামাজ পড়তে যেতেন। নামাজ শেষে পশু কুরবানি করার পর খিচুড়ি, বেগুন ভাজি, ডিম ভুনা, সেমাই, সুজি, মিষ্টি, পায়েস দিয়ে আহার করতেন। ওই কুরবানির গোসত ছাড়া অন্য কোন গোসত রান্না হতো না। আমরা এই ঈদে ঈদ সালামির পিছনে না ঘুরে পশু কুরবানি দেখতাম। গোছল শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গরুগুলোকে বাইর বাড়ি বেঁধে রাখা হতো। ঈদের নামাজ শেষে স্থানীয় মাদ্রাসা থেকে ধার দেওয়া বড় বড় ছুরি হাতে নিয়ে হুজুররা আসতেন। আমরা অতো বড় ছুরি দেখে ভয় পেতাম, সরে যেতাম, আবার লুকিয়ে লুকিয়ে কুরবানি করা দেখতাম। পশু কুরবানির সময় যখন ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতো, তাই দেখে আমরা ভয়ে ছুটে বাড়ির ভেতর পালিয়ে যেতাম।
ছোটবেলায় দেখেছি, গ্রামে যারা কুরবানি দিতেন, তাদের সকলের বিলানোর জন্য নির্ধারিত কুরবানির গোসত মসজিদের মাঠে এক জায়গায় জড়ো করতেন এবং গ্রামে যারা কুরবানি দিতেন না, তাদের সকলের নাম লিষ্ট করে তাদের বাড়ি বাড়ি গোসত পৌঁছে দিতেন। যার যার কুরবানির বাকি গোসত বাড়িতে আনার পর উঠোনে বস্তা বিছিয়ে তার উপর কলার পাতায় আবার তিন ভাগে ভাগ করতেন। সেখান থেকে পাড়ার গরীব মিসকিন একভাগ, আত্মীয় স্বজন একভাগ এবং নিজেদের রান্নার জন্য একভাগ গোসত রাখতেন। তখন আসলে এখনকার মতো গোসত সংরক্ষণের জন্য ঘরে ঘরে ফ্রিজ ছিল না বিধায় বেশির ভাগ গোসত প্রতিবেশীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। যেটুকু নিজেদের জন্য থাকতো, তার মধ্য থেকে কিছু গোসত আম্মা লবন, হলুদ, তৈল দিয়ে আলাদা করে জাল দিয়ে রাখতেন, আর কিছু রান্না করতেন। যা রান্না হতো তা আবার পরদিন লোহার কড়াইতে সরিষার তেল, শুকনো ঝাল, রসুন কুঁচি দিয়ে ঝুড়ি করে ভাজতেন। আম্মার হাতের সেই ভাজা গোসত যেন অমৃত সমান মনে হতো। এখনো চোখ বন্ধ করলেই আম্মার হাতের সেই স্বাদ অনুভব করি। আহা আম্মা! আহা আব্বা! আহা কুরবানির ঈদ।
এখন ঘরে ঘরে ফ্রিজ, বাড়ি বাড়ি ছাদ। সেই আঙিনা, সেই মাঠ কোথায়? ফ্রিজের বাড়িতে কোথায় সেই ভাজা গোসতের স্বাদ। কোথায় কলার পাতা, বড় কচুর পাতায় বাড়ি বাড়ি গোসত পৌঁছে দেওয়ার আনন্দ। কলা পাতা, কচু পাতার দিন শেষে এখন পলিথিনের যুগ, দানÑপ্রতিদানের কাল শেষে এখন ফ্রিজের যুগ, পাড়া প্রতিবেশি তো দূরের কথা, এখন পাশের ফ্ল্যাটের কে কাকে চিনি আমরা?
তবুও ঈদ আসে ফিরে ফিরে বারবার। ত্যাগ তিতিক্ষার ঈদ আসে,
কুরানির গরু আসে, ছাগল আসে বাড়িতে, ছাদ, গাড়ি বারান্দায়, আঙিনায়
সে খবর দিন শেষে কে রাখে, কে আনন্দ পায় আগের মতোই আরবার?
[লেখক: কবি, গবেষক, কথাশিল্পী, অধ্যক্ষ, তালবাড়ীয়া ডিগ্রি কলেজ, যশোর। ০১৯১৩-৮১০৭৪৮]

নীরবতার গায়ে
জড়ানো কবিতা
আ র শি গা ই ন
কলেজ তখন ছিল অনিরুদ্ধের একান্ত আকাশ, আর সেই আকাশে শব্দেরা উড়ে বেড়াত কবিতা হয়ে। অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে খেলার মাঠের কোচ পর্যন্ত জানত, “ছেলেটা কবিতা লেখে”—মনে হয় যেন সে কোনো অলিখিত রাজকীয় সম্মানে ভূষিত।
বন্ধু-সঙ্গীর ভিড়ে হঠাৎ একদিন তার চোখে এসে থেমে যায় একটি মেয়ের চোখ। নাম জানার আগেই সে তার জন্য এক শব্দ খুঁজে নেয়—“নীরু”।
“নাম কী তোমার?” “পৌশি।” “সে যাই হোক… তুমি আমার নীরু। আমার কবিতার নীরু।”

পৌশি হেসে ওঠে—তুষারের মতো নরম সেই হাসি, যেন শব্দের ভেতর জমে থাকা বসন্ত হঠাৎই ফেটে পড়ে।
তারপর, অনিরুদ্ধর খাতায় জমে উঠতে থাকে নীরুর চোখের বর্ণনা, ঠোঁটের নীরবতা, কপালের ঘামে ছুঁয়ে থাকা একটি চৈত্র দুপুর। কবিতা ছাপা হলে, পৌশি পড়ে—আবৃত্তির মতোই বলে ওঠে, “তুমি এমন করে লেখো কী করে কবি?” অনিরুদ্ধ জবাব দেয় না—চোখে চোখ রেখে শুধু চুপ করে বলে ওঠে এক না-বলা ভাষায়—”তোমার জন্যই তো লেখা।”
তবুও ভালোবাসার উচ্চারণ অনিরুদ্ধর কণ্ঠে উঠে আসে না। কারণ সে জানে, তার ভালোবাসায় টিউবের ভাঙা প্যানের মতো চিরে আছে দরিদ্রতার দাগ। সে চুপ থাকে। আড়ালে ভালোবাসে। শুধু লেখে।
কিন্তু একদিন পৌশিই বলে ফেলে, “অনিরুদ্ধ… আমি তোমায় ভালোবাসি।”
সেই মুহূর্তটা যেন কোনো কবিতার শেষ লাইন হয়ে হৃদয়ে পাথরের মতো গেঁথে থাকে। তাদের গল্প শুরু হলেও, পরিণতির ছায়া তখনই ঘনিয়ে আসে।
বাড়ির চাপে একদিন পৌশিকে বিয়ে দেওয়া হয় এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে—ধনী, প্রাপ্তবয়স্ক, কিন্তু কবিতা বোঝে না। বিয়ের আগের দিন পৌশি শুধু বলে, “মাফ করে দিও কবি… তোমার নীরু নিজেকে রাখতে পারল না।”
তারপর নীরবতা দীর্ঘতর হয়। কবিতা লেখে অনিরুদ্ধ, কিন্তু সেখানে আর পৌশির চোখের ছায়া থাকে না। তার খাতায় জমে ওঠে শুধুই বিরহের বাতাস।
বছর চারেক পর এক পত্রিকার জন্য কাজ করতে গিয়ে মর্গে যেতে হয় তাকে—যশোর সদর হাসপাতাল। আত্মহত্যা করা এক মহিলার ছবি তুলতে হবে রিপোর্টের প্রয়োজনে। পর্দা সরাতেই যে দৃশ্যের মুখোমুখি হয়, তাতে তার সময় থেমে যায়।

শুয়ে আছে পৌশি। নিথর। ঠোঁটে কোনো প্রশ্ন নেই, চোখে কোনো উজ্জ্বলতা নেই—তবুও তার মুখের রেখায় যেন অনিরুদ্ধ পড়ে নিতে পারে, “তুমি কি তখনও আমাকে নীরু বলে ডাকো?”
তার নিস্পন্দ শরীরের পাশে বসে অনিরুদ্ধ কাঁপা হাতে ছুঁয়ে দেখে সেই কপোল, যেটা নিয়ে সে একদিন কবিতা লিখেছিল—“তোমার কপোলে সাঁঝ নেমে আসে…” গলায় দাগ, চোখে অপূর্ণ এক যন্ত্রণার ছায়া। যেন বেঁচে থাকতে কেউ বুঝতে পারেনি, সে একদিন কবির কবিতা ছিল।
ব্যাগ থেকে পুরনো কবিতার খাতা বের করে অনিরুদ্ধ পড়ে— “নীরু, তোমায় ভালোবাসি—এই শব্দটুকু কখনো বলা হয়নি। তাই আমি কেবল কবিতা লিখে গেছি। তুমি পড়ে হাসতে, আর আমি ভেতরে ভেঙে যেতে যেতে আরও লিখতাম।”
মর্গের নীরবতায়, এক নির্জন দুপুরে, অনিরুদ্ধ সেই মৃত চোখের দিকে তাকিয়ে ভাবে—“তুমি কি জানো, কবিতারা কাঁদে?”
পুলিশি রিপোর্টে লেখা—”পারিবারিক কলহ ও মানসিক অবসাদে আত্মহত্যা”। কিন্তু অনিরুদ্ধ জানে—এই মৃত্যু আসলে এক কবিতার না বলা শেষ পঙ্ক্তি।
সে ছবি তোলে না। রিপোর্ট জমা দেয় না। পত্রিকায় ছাপে না কোনো সংবাদ। শুধু ছাপে—একটি কবিতা—
“মৃত্যু সবসময় ফাঁসির দড়ি হয় না, কখনো তা হয়ে ওঠে অব্যক্ত প্রেমের শ্বাসরুদ্ধ পঙ্ক্তি, যেখানে কবিতার নাম ছিল ‘নীরু’, আর পাঠক ছিল না কেউ।”
তারপর আর কোনো কবিতা লেখে না অনিরুদ্ধ। শুধু মাঝে মাঝে হাওয়ায় কান পাতলে শোনা যায়— “নীরু তো আমার নাম না…” আর এক ক্লান্ত কণ্ঠ ফিসফিসিয়ে জবাব দেয়— “তবুও, আমার কবিতায় তুমি চিরকাল নীরু। চিরকাল…”